হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির খড়গ : আসামের এনআরসি এবং বাংলাদেশ
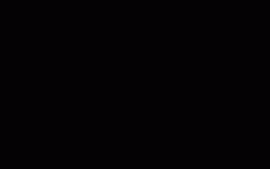
কিশোর শিক্ষার্থীদের নিরাপদ সড়ক দাবীর আন্দোলনে ঢাকাসহ সারাদেশে তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা ও অনিশ্চয়তা দেখা যাচ্ছিল,
কামরুল হাসান দর্পণ
ঢাকায় আসা, ঢাকায় থাকা, ঢাকায় একবার ঘুরে যাওয়া একটা নেশার মতো। ঢাকায় যারা থাকেন, তারা যেমন ঢাকা ছেড়ে যেতে চান না, তেমনি ঢাকায় একবার যারা ঢুকে পড়েন, তারা আর ফিরতে চান না। ঢাকা যতই সমস্যায় জর্জরিত হোক, নাগরিক সুযোগ-সুবিধা যতই কম হোক, তথাপি ঢাকাবাসী ঢাকায়ই থাকতে চান। ঢাকা ছেড়ে কিছু দিন বাইরে থাকলেই হাঁপিয়ে ওঠেন। কখন প্রাণের শহর, প্রিয় শহর ঢাকায় ফিরবেন, এ নিয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন। ঢাকা ছাড়ার অর্থ যেন তাদের কাছে পুরো পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। এটা আসলে অভ্যস্ততার ব্যাপার। অনেক সময় মানুষ চরম দুরবস্থার মধ্যেও নিজেকে মানিয়ে নেয়। ঢাকায় যারা বসবাস করেন এবং যারা ঢাকাগামী হন, তারা ঢাকার কঠিন জীবন এবং দুরবস্থার কথা মেনে নিয়েই থাকেন এবং আসেন। এর কারণ ঢাকা তাদের স্বপ্ন। যারা আসেন তারা মনে করেন ঢাকা আসতে পারলেই তাদের জীবনধারা বদলে যাবে। স্বপ্ন পূরণ হবে। এই যে মানুষের ঢাকামুখী হওয়া, এটা যে ঢাকাকে বসবাসের আরও অনুপযোগী করে তুলছে এবং তাদের কষ্টের মধ্যে পড়তে হবে, এটা তাদের মাথায় থাকে না। তারা মনে করেন, কোনো রকমে ঢাকায় ঢুকতে পারলেই হলো, জীবন বদলে যাবে। এর ফলে প্রতিদিন ঢাকায় মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হিসাব অনুযায়ী, প্রতিদিন ঢাকায় মানুষের আগমন ঘটছে ১৭০০ জন। অবশ্য এ সংখ্যাটি পুরোপুরি সঠিক নয়। কোনো কোনো হিসাবে সংখ্যাটি আড়াই হাজারের বেশি। এ হিসাবে ঢাকায় মাসে যুক্ত হচ্ছে ৫০ থেকে ৭৫ হাজার মানুষ। পৃথিবীর আর কোনো শহরে এত অধিক সংখ্যক মানুষের যুক্ত হওয়ার নজির খুব কমই রয়েছে। বিবিএসের হিসাবে ঢাকার বর্তমান লোকসংখ্যা ১ কোটি ৭০ লাখ। জাতিসংঘের ইউএনএফপির হিসাবে পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল শহরগুলোর তালিকায় ঢাকা ১১তম। তবে আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যার দিক থেকে এটি পৃথিবীর এক নম্বর জনঘনত্বের শহর। এখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৪৩ হাজার ৫০০ জন মানুষ বসবাস করে। এ যেন মানুষের গিজগিজ করে বসবাস। যে হারে ঢাকায় মানুষের আগমন ঘটছে, তাতে আগামী কয়েক বছরে এর অবস্থা কী হবে, তা অনুমান করা কঠিন নয়। মানুষের ভারে, পদচারণায়, ধারণ ক্ষমতার অভাবে কি ঢাকা দেবে যাবে বা ভেঙে পড়বে? হ্যাঁ, ভেঙেও পড়তে পারে, দেবেও যেতে পারে। আল্লাহ না করুন, একটা মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প হলে ঢাকা আস্ত থাকবে না। মৃত্যুপুরীতে পরিণত হবে। এর বেশির ভাগ সুউচ্চ ভবন ভেঙে পড়বে, লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু হবে এমনকি ভূমি ধসে কোনো কোনো এলাকা দেবে যেতে পারে। এমন প্রাকৃতিক বিপর্যয় সামনে থাকা সত্ত্বেও ঢাকামুখী মানুষের আগমন যেমন কমেনি, তেমনি ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছাও কারো নেই। আবার ঢাকার এ অবস্থা দূর করার তেমন কোনো নীতি ও পরিকল্পনাও ঢাকার কর্তৃপক্ষের নেই। যেমন আছে তেমন চলতে থাকুকÑ এমন একটা প্রবণতা সবসময়ই রয়েছে। প্রশ্ন আসতে পারে, ঢাকায় মানুষের এই আগমনের জন্য কি কেবল ঢাকাগামী মানুষরাই দায়ী? তারা কি সাধ করে ঢাকার কষ্টের জীবনে জড়াতে চায়? এসব প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, কেউ সাধ করে কষ্টের জীবনে জড়াতে চায় না। এর জন্য দায়ী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। কারণ রাষ্ট্র ঢাকার মধ্যেই মৌচাকের মতো সকল সুযোগ-সুবিধা মধু কেন্দ্রীভূত করে রেখেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন-আদালত, প্রশাসন, কলকারখানা থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক কর্মকা-ের কেন্দ্রবিন্দু করা হয়েছে ঢাকাকে। ফলে মানুষ এখানে ছুটে আসবে, এটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া রাজধানীতে বসবাস এবং উন্নত জীবনের ছোঁয়া পাওয়ার একটা লোভ তো আছেই।
দুই.
ঢাকাকে বলা হয় মেগাসিটি। সাধারণত যে শহরের লোকসংখ্যা এক কোটি ছাড়িয়ে যায়, সেই শহর এই খেতাব লাভ করে। ঢাকার লোকসংখ্যা যেভাবে বাড়ছে, তাতে আগামী কয়েক বছরে এর জনসংখ্যা দুই কোটি ছাড়িয়ে যাবে। ডাবল মেগাসিটিতে পরিণত হবে। এই বিপুলসংখ্যক রাজধানীবাসীর ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা কীভাবে নিশ্চিত করা হবে, এ নিয়ে কোনো পরিকল্পনার কথা আমরা শুনি না। পরিকল্পনা আছে কিনা, তাও জানি না। বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, ঢাকায় যারা থাকেন এবং আসেন, তারা নিজেরাই নিজেদের বসবাসের জায়গা করে নেন। এতে পরিকল্পনার প্রয়োজন পড়ছে না। অথচ যে কোনো রাজধানী গড়ে তোলা হয় পরিকল্পিতভাবে। এ জন্য কর্তৃপক্ষ আছে। যে কেউ চাইলেই ইচ্ছামতো ঘরবাড়ি বা ছাপড়া তুলে বসবাস করতে পারে না। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পরিকল্পিতভাবে সম্প্রসারণের কাজটি করে। ঢাকাকে দেখলে মনে হবে, এর সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে কোনো কর্তৃপক্ষ নেই। যে যেভাবে যেদিকে পারছে ঢাকাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এগোচ্ছে তো এগোচ্ছেই। থামাথামি নেই। থামানোর চেষ্টাও নেই। এই সম্প্রসারণ কাজ করতে গিয়ে নগরীর প্রাকৃতিক যে বৈশিষ্ট্য থাকা অপরিহার্য, তা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ঢাকা পরিণত হচ্ছে ইট, কাঠ, পাথরের নগরীতে। বলা হয়, ঢাকার মতো প্রাকৃতিক সুষমাম-িত রাজধানী বিশ্বে খুব কম আছে। এটি এমন এক শহর, যার ভেতর দিয়ে এক সময় স্বচ্ছ প্র¯্রবণ বহমান ছিল। জালের মতো খাল আর চতুর্দিকে নদী। ঘরবাড়ি, অফিস-আদালতের পাশ দিয়ে স্বচ্ছ বারিধারা বয়ে যেত। পানিতে ভবনের ছায়া ও বিদ্যুতের আলো ঢেউ খেলে যেত। এসব এখন কেবল কল্পনায় পরিণত হয়েছে। এখন কেউ কি কল্পনা করতে পারে, এই ঢাকায় একসময় ছোট-বড় প্রায় ৪২টি খাল ছিল? এ প্রজন্মের কাছে তো তা স্বপ্নের মতো। তারা কেবল শুনছে, এই সুউচ্চ ভবনটি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে বা এই সড়কটি যেখান দিয়ে গিয়েছে, এসবই খালের ওপর গড়ে উঠেছে। তাদের কি বিশ্বাস করানো যাবে, আজকের যে গুলশান, সেখানে বাড্ডা এলাকায় এক সময় নৌকা ভিড়ত? আজকের যে সুরম্য বসুন্ধরা সিটি মার্কেট, এ জায়গাটি ছিল বিশাল একটি ঝিল? সেখানে শাপলা ফুটত, নৌকা চলত। এখন ঢাকা শহরে যেসব লেক দেখা যায়, এগুলো মূলত সেসব খাল বা নদীর রেপ্লিকা মাত্র। এগুলো কৃত্রিমভাবে গড়ে তোলা হয়নি। প্রাকৃতিকই ছিল। শহরের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীতে গিয়ে মিশেছিল। কেবল দখলদারিত্বের কবলে পড়ে আবদ্ধ জলাভূমিতে পরিণত হয়েছে। যদি এসব খাল রক্ষা করা যেত, তাহলে ঢাকা শহরের চেহারাটা কেমন হতো? কাচঘেরা সুউচ্চ ভবন এবং এলইডি লাইটের আলোয় কী ঝলমলই না করত! ঢাকার আজকের যে অসীম সমস্যা তা থেকে অনেকটাই মুক্ত থাকা যেত। বুকভরে মানুষ সতেজ নিঃশ্বাস নিতে পারত। মানুষকে শীষা, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোঅক্সাইড মিশ্রিত বিষাক্ত বায়ু সেবন করে হৃদরোগ, শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিসসহ জীবন বিনাশক মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হতে হতো না। খুব স্বাভাবিক হিসেবে যদি ধরা হয়, প্রায় দুই কোটি মানুষ নিঃশ্বাসের সাথে যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়ছে, এই বিপুল পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড শুঁষে নেয়ার মতো সবুজ গাছগাছালি রাজধানীতে নেই। এর সাথে গাড়ির বিষাক্ত ধোঁয়া যুক্ত হয়ে পরিবেশকে কী পরিমাণ দূষিত করে তুলেছে, তা কি কল্পনা করা যায়? এ ছাড়া পয়োনিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার যে দুর্দশা, তাতে পরিস্থিতিকে কী দুর্বিষহই না করে তুলছে! এসব সমস্যা সমাধানে যে ধরনের কর্তৃপক্ষ এবং তার সুষম পরিকল্পনা থাকা দরকার, তা ঢাকা শহরে নেই। যারা আছে, তারা তাদের সক্ষমতা আজ পর্যন্ত প্রমাণ করতে পারেননি। তারা নিজেরাই নানা অপরিকল্পনা ও সমস্যার মধ্যে জড়িয়ে আছে। তাদের অজুহাতের শেষ নেই। এই সক্ষমতার অভাব এবং অজুহাত দিয়েই বছরের পর বছর তারা পার করে দিচ্ছে। সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলো যদি তাদের কাজটুকু যথাযথভাবে করত, তাহলেও অনেক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হতো। বিশেষ করে দুই সিটি করপোরেশন, যাদের ওপর ঢাকার অধিকাংশ সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব, তারা যদি একটু তৎপর ও পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করত, তবে ঢাকা যে দুরবস্থার দিকে ধাবিত, তার গতি কিছুটা হলেও টেনে ধরা যেত। পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা শহরটির মতো যদি কিছুটা শৃঙ্খলার মধ্যে আনা যেত, তবে ঢাকা শহরের চেহারা অনেকটাই বদলে যেত। কলকাতার সমস্যার অন্ত নেই, তবে সেখানে সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আন্তরিক প্রচেষ্টা রয়েছে। এ আন্তরিকতার প্রমাণ পাওয়া যায় পরিবর্তনের দৃশ্যমান কর্মকা-ের মাধ্যমে। সেখানের মানুষ আশাবাদী হয়ে উঠেছে, সমস্যা সমাধানে যেহেতু হাত দেয়া হয়েছে, সময় লাগলেও তা সমাধান হবে। ঢাকাবাসীর চোখে এ ধরনের আশাব্যঞ্জক কোনো পদক্ষেপ আজ পর্যন্ত চোখে পড়েনি। একটি আধুনিক রাজধানীর কি সুযোগ-সুবিধা থাকে, তা তারা যেমন জানেন না, তেমনি সমস্যাকে নিত্যসঙ্গী হিসেবে মেনে নিয়েই তারা বসবাস করছেন।
তিন.
ঢাকার অসংখ্য সমস্যার মধ্যে যেটি প্রধান হয়ে উঠেছে, তা হচ্ছে যানজট। প্রতি মুহূর্তে এ সমস্যায় পড়ছে না, এমন মানুষ নেই। যানজটে মানুষের কী পরিমাণ ক্ষতি হয়, তার হিসাব বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন সময়ে দিয়েছে। বুয়েটের এক গবেষণায় বলা হয়েছে, যানজটের কারণে বছরে ২২ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়, বেসরকারি গবেষণা সংস্থা পিপিআরসি বলেছে ২০ হাজার কোটি টাকার কথা। সর্বশেষ জাতিসংঘের ইউএনডিপি এক গবেষণায় বলেছে, যানজটে বছরে ক্ষতি হয় ৩৫ হাজার ১০০ কোটি টাকা। ইউএনডিপি এ হিসাবের মধ্যে দেখিয়েছে, যানজটের কারণে দৈনিক ৪০ লাখ কর্মঘণ্টা নষ্ট হওয়ায় আর্থিক ক্ষতি হয় ৩০০ কোটি টাকা। এর সাথে যুক্ত হয়েছে যানবাহনের পুড়ে যাওয়া বাড়তি জ্বালানির মূল্য (যানজটে বাসে ৩ গুণ তেল পোড়ে) এবং নগরবাসীর স্বাস্থ্যহানির আর্থিক মূল্য। যানজটে বছরে যে ক্ষতি হয় তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রতি বছর একটি করে পদ্মা সেতু নির্মাণ করেও অতিরিক্ত অর্থ উদ্বৃত্ত থেকে যাবে। এভাবে বছরের পর বছর ধরে যে ক্ষতি হচ্ছে, এ ক্ষতি যদি অর্ধেকেও নামিয়ে আনা যায়, তবে প্রতি দুই বছরে একটি করে পদ্মা সেতু নির্মাণ করা সম্ভব। এ হিসাবে, যে পদ্মা সেতু নিয়ে আমাদের এত গর্ব, তা কি যানজটে ক্ষতির কাছে ম্লান হয়ে যায় না? আমরা পদ্মা সেতু নির্মাণে যেভাবে নিজস্ব অর্থায়ন এবং দ্রুতগতিতে কাজ সমাপ্ত করার দিকে মনোযোগী হয়েছি, এ মনোযোগ যদি যানজট নিরসনের দিকে দিতাম, তাহলে আমাদের অর্থনীতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াত! যে বিনিয়োগ নিয়ে এত হা-হুতাশ ও অর্থনৈতিক টানাপড়েন এবং জনগণের পকেট থেকে নানা উপায়ে সরকারের পয়সা বের করে নেয়ার ফন্দি-ফিকির, তা করার দরকার পড়ত কি? এমনকি যে ঘাটতি নিয়ে লাখ লাখ টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়, সে ঘাটতি কি থাকত? সরল হিসাবে যদি ধরা হয়, তবে যানজটের ক্ষতি অর্ধেকে নামিয়ে আনা গেলে চার বছরের মধ্যে ঘাটতিবিহীন একটি বাজেট ঘোষণা দেয়া সম্ভব হতো। যাই হোক, যানজটের ক্ষতির মাত্রা বলে শেষ করা যাবে না। এর ক্ষতি বহুমাত্রিক। যানজটে পড়ার ভয়ে কর্মজীবী মানুষ থেকে শুরু করে প্রত্যেকের স্বাভাবিক জীবন ও কর্মকা- প্রতিদিনই ব্যাহত হচ্ছে। ঢাকায় যারা বসবাস করেন, তারা জীবনযাত্রা পরিবর্তন করে এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। যারা ঢাকায় আসেন, তাদের জীবনযাত্রা অনিবার্যভাবেই পরিবর্তন করতে হয়। যেখানে কর্মস্থলে যাওয়ার স্বাভাবিক সময় আধাঘণ্টা, সেখানে তাকে দুই ঘণ্টা আগে থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। তা না হলে কোনোভাবেই চাকরি-বাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্য ঠিকমতো চালানো সম্ভব নয়। যানজটের কারণ মোটামুটি সবারই জানা। তবে পুলিশের পক্ষ থেকে ১৯টি কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, ট্র্যাফিক আইন না মানা ও সঠিকভাবে প্রতিপালন না করা, যত্রতত্র কার পার্কিং এবং কার পার্কিংয়ের জায়গায় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, যেখানে সেখানে গাড়ি থামিয়ে যাত্রী ওঠানামা করা, রাস্তা ও ফুটপাত দখল, ট্র্যাফিক পুলিশের যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাব ইত্যাদি। এর বাইরে মূল যে সমস্যা তা হচ্ছে, রাজধানীর রাস্তার তুলনায় অধিক সংখ্যক গাড়ি চলাচল। বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, যেখানে একটি আদর্শ শহরে ২৫ ভাগ সড়ক থাকে, সেখানে ঢাকা শহরে রয়েছে মাত্র ৮ ভাগ। আবার এই ৮ ভাগের মধ্যে কার্যকর রাস্তা হচ্ছে আড়াই ভাগ! এই কার্যকর রাস্তা দিয়ে সোয়া দুই লাখ গাড়ি চলাচল করতে পারলেও এখানে চলছে ৯ লাখ। তার ওপর প্রতিদিন ৩১৭টি গাড়ি রাস্তায় নামছে। এ যদি হয় পরিস্থিতি, তবে যানজট সৃষ্টি না হয়ে উপায় আছে? আরও কারণ রয়েছে। নগরীতে লোকসংখ্যার অনুপাতে যে পরিমাণ গণপরিবহন থাকার কথা তা একেবারেই নেই। অথচ যানজট সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য এবং লোকজনের যাতায়াতে পর্যাপ্ত গণপরিবহনের বিকল্প নেই। সারা বিশ্বেই গণপরিবহনের ওপর বেশি জোর দেয়া হয়। বাংলাদেশই কেবল ব্যতিক্রম। এক গবেষণায় দেখানো হয়েছে, নগরীতে ৬০ ভাগ মানুষ হেঁটে চলেন। রিকশায় চলেন ১৯ ভাগ। বাস ও অটোরিকশায় চলেন ১৬ ভাগ। আর প্রাইভেট কারে চড়েন মাত্র ৫ ভাগ। অর্থাৎ ৫ ভাগ মানুষের প্রাইভেট কারের জন্য ঢাকার যানজট তীব্র হয়ে রয়েছে এবং প্রাইভেট কারেরই অনুমোদন দেয়া হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। একটি প্রাইভেট কারে ড্রাইভারসহ দুজন থেকে পাঁচজন চড়তে পারে। বেশির ভাগ সময় শুধু দুজনই চড়েন। বাকি তিনজনের জায়গা খালিই পড়ে থাকে এবং রাস্তার বিরাট একটা অংশ দখলে চলে যায়। আবার এসব গাড়ি রাস্তার ওপর পার্কিং করার কারণেও যানজট সৃষ্টি করে চলেছে। এ পরিস্থিতি যদি হয়, তবে যানজট কোনোকালেই কমবে না। ঢাকার যানজট কমাতে হলে প্রাইভেট কারের অনুমোদনের সংখ্যা কমাতে হবে। যাদের একাধিক প্রাইভেট কার রয়েছে, তাদের একটির মধ্যে সীমাবদ্ধ করা প্রয়োজন এবং তার জায়গায় আধুনিক, আরামদায়ক ও শৃঙ্খলাবদ্ধ গণপরিবহনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা জরুরি। একবার যোগাযোগ ও সেতুমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছিলেন এক পরিবারের এক প্রাইভেট কার নীতির। এ ঘোষণার বাস্তবায়ন দেখা যায়নি। নীতিটি খুবই ভালো ছিল। বাস্তবায়ন করা গেলে যানজট কিছুটা হলেও সহনীয় পর্যায়ে আসত। কেন এর বাস্তবায়ন হলো না, তা বোধকরি ব্যাখ্যা করে বলার অবকাশ নেই।
চার.
ঢাকাকে বাসযোগ্য করার তাগিদ নগরবিদরা বহুদিন ধরেই দিচ্ছেন। তারা প্রতিনিয়ত এন্তার পরামর্শ ও পরিকল্পনার কথা বাতলাচ্ছেন। তাদের এ পরামর্শ কেবল শোনা যায়, শুনতে ভালো লাগে। তবে যাদের শোনার কথা এবং বাস্তবায়ন করার কথা, তারা শোনে না। যানজট নিরসন এবং সৌন্দর্যবর্ধনে এক ফুটপাত দখলমুক্ত করা নিয়ে কত কী ঘটে গেল, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। গুলিস্তানের ফুটপাত দখলমুক্ত করা নিয়ে এক ধরনের ইঁদুর-বেড়াল খেলা আমরা প্রায় সময়ই দেখি। ফুটপাত আর দখলমুক্ত হয় না। দখলকারীরা কত শক্তিশালী যে সিটি করপোরেশনও তাদের কাছে অসহায় হয়ে পড়ে। তবে আমরা ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র আনিসুল হকের ইচ্ছা এবং উদ্যোগ দেখে আশাবাদী হচ্ছি। তিনি তার অংশকে বাসযোগ্য করার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। পরিবেশ সবুজায়নের কার্যক্রম এবং পরিচ্ছন্নতার অভিযান শুরু করেছেন। যানজট নিরসনে দখলকৃত জায়গা উদ্ধার করে সাফ করছেন। সাতরাস্তা থেকে গাজীপুর পর্যন্ত নিয়মমাফিক যান চলাচলে ইউলুপ তৈরির উদ্যোগ নিয়েছেন। এমনকি যেসব দোকানপাট ও বাড়িঘর অপরিকল্পিতভাবে এবং ফুটপাত দখল করে তৈরি করা হয়েছে, সেগুলো ভেঙে দিচ্ছেন। তার এই দৃশ্যমান কার্যক্রম দেখে আমরা আশাবাদী হয়ে উঠছি। মনে হচ্ছে কিছু একটা হবে। ঢাকাকে মানুষের চাপমুক্ত রাখতে এবং ঢাকাগামী মানুষের ¯্রােত ঠেকাতে বিচার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যাংকিং সেবাসহ প্রশাসনিক কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণের কথা বহুদিন ধরেই বিশেষজ্ঞরা বলে আসছেন। এসব সরকারের সিদ্ধান্তের ব্যাপার। সরকার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে অনেক কিছুই করেছে। আমরা মনে করি, ঢাকাকে হালকা এবং আধুনিকভাবে গড়ে তুলতে হলে সরকারকে বিকেন্দ্রীকরণের কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অন্যান্য বিভাগীয় শহর ও প্রধান জেলা শহরগুলোতে ঢাকার মতো সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির উদ্যোগ নিতে হবে। ঢাকায় আর কোনো কলকারখানা স্থাপনের অনুমোদন দেয়া যাবে না। বিভিন্ন আঞ্চলিক শহরে শিল্পকারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ করতে হবে, যাতে ঢাকার বাইরে কর্মসংস্থান সৃর্ষ্টি হয় এবং জীবিকার সন্ধানে মানুষকে ঢাকামুখী না হতে হয়। এ জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা করতে হবে এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী দ্রুত কাজ শুরু করতে হবে। তা না হলে আমরা যে উন্নতি করছি, ঢাকার দুরবস্থা দেখে কেউই তা মনে করবে না।
![]() দৈনিক ইনকিলাব সংবিধান ও জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাই ধর্ম ও রাষ্ট্রবিরোধী এবং উষ্কানীমূলক কোনো বক্তব্য না করার জন্য পাঠকদের অনুরোধ করা হলো। কর্তৃপক্ষ যেকোনো ধরণের আপত্তিকর মন্তব্য মডারেশনের ক্ষমতা রাখেন।
দৈনিক ইনকিলাব সংবিধান ও জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাই ধর্ম ও রাষ্ট্রবিরোধী এবং উষ্কানীমূলক কোনো বক্তব্য না করার জন্য পাঠকদের অনুরোধ করা হলো। কর্তৃপক্ষ যেকোনো ধরণের আপত্তিকর মন্তব্য মডারেশনের ক্ষমতা রাখেন।