হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির খড়গ : আসামের এনআরসি এবং বাংলাদেশ
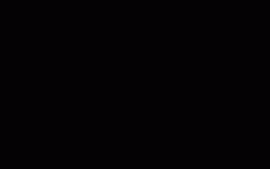
কিশোর শিক্ষার্থীদের নিরাপদ সড়ক দাবীর আন্দোলনে ঢাকাসহ সারাদেশে তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা ও অনিশ্চয়তা দেখা যাচ্ছিল,
কামরুল হাসান দর্পণ : নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। কোনোভাবেই বিতর্ক তার পিছু ছাড়ছে না। নির্বাচনের আগে তিনি যেমন গোঁয়ার-গোবিন্দর মতো নানা ধরনের উগ্র বক্তব্য দিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করেছেন, তেমনি নির্বাচনে বিজয় লাভের পর তার বিজয় নিয়ে বিতর্ক উঠছে। ভোট পুনঃগণনা থেকে শুরু করে সম্প্রতি সিআইএ প্রতিবেদন দিয়েছে, সাইবার হামলার মাধ্যমে ট্রাম্পকে জিততে সহায়তা করেছে রাশিয়া। জবাবে ট্রাম্পও তার স্বভাবসুলভ বক্তব্যের মাধ্যমে কটাক্ষ ও তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য যারাই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে তাদের তিনি এক হাত নিয়ে নেন। যেমন সম্প্রতি প্রকাশিত সিআইএ’র প্রতিবেদন প্রকাশের জবাবে তিনি বলেছেন, ‘এরা তো সেসব লোক, যারা বলেছিল সাদ্দাম হোসেনের কাছে মারাত্মক গণবিধ্বংসী অস্ত্র রয়েছে। এসব ভুয়া কথা। এবারের নির্বাচন হয়েছে ইতিহাসের বৃহত্তম ইলেক্টোরাল কলেজের জয়।’ ট্রাম্প যতই এসব অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করুন না কেন, বারাক ওবামা কিন্তু সিআইএ’র প্রতিবেদন গুরুত্বের সাথে নিয়ে তদন্ত এবং তিনি ক্ষমতায় থাকতে থাকতে প্রতিবেদন জমা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ আমেরিকা তার নির্বাচন পদ্ধতির স্বচ্ছতা ও বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে চায়। তদন্তে কী হবে না হবে, সেটা পরের কথা। আমেরিকার নির্বাচন নিয়ে যে বিতর্ক উঠেছে, এটা বৃহত্তম এই গণতান্ত্রিক দেশটির জন্য অত্যন্ত মর্যাদাহানিকর। এর আগে কোনো নির্বাচন নিয়ে এত বিতর্ক হয়নি। এক ট্রাম্প নির্বাচনে দাঁড়িয়ে আমেরিকার নির্বাচনী ব্যবস্থাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলেছেন। ভোটের আগে তিনি ভোট কারচুপি হতে পারে, নিজে জিতলে কারচুপি হয়নি বলে মন্তব্য করে আমেরিকার নির্বাচনী পদ্ধতিকে বিরাট ধাক্কা দেন। এ ছাড়া প্রতিপক্ষ হিলারি ক্লিনটনের বিরুদ্ধে হেন কোনো অশ্রাব্য মন্তব্য নেই, যা তিনি করেননি। নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর তো তার বিরুদ্ধে নিউ ইয়র্কসহ আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ স্টেটগুলোতে বিক্ষোভ মিছিল পর্যন্ত হয়েছে। আমেরিকার ইতিহাসে নির্বাচিত কোনো প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে এমন গণবিক্ষোভ আর হয়নি। ট্রাম্প যেন আপাদমস্তক একজন বিতর্কিত ব্যক্তি যিনি বিজয়ী হয়েও বিতর্কের বাইরে যেতে পারছেন না। প্রতিনিয়ত তাকে অনাকাক্সিক্ষত পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে। তার বিজয় বিতর্কিত ও প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে। রাশিয়া সাইবার হামলার মাধ্যমে নির্বাচনের ফলাফল পাল্টে দিয়েছে বলে সিআইএ যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, এ ধরনের একটি আলোচনা নির্বাচনের পরপরই আমেরিকার অধিকাংশ জনগণের মধ্যে ছিল। সে সময় মেরিল্যান্ডে বসবাসরত আমার এক আত্মীয় টেলিফোনে এ কথা জানিয়েছিলেন। তিনি যেমন বিশ্বাস করতে পারেননি, আমারও বোধগম্য হচ্ছিল না। প্রশ্ন জাগে, আমেরিকার মতো উন্নত প্রযুক্তির দেশে জাতীয় নির্বাচনের ফলাফল সাইবার হামলার শিকার হয় কী করে? ফলাফল উল্টে দেয়ার মতো ঘটনা কি বিশ্বাসযোগ্য? সিআইএ’র প্রতিবেদন প্রকাশের পর মনে হচ্ছে, হলেও হতে পারে। বিশেষ করে আমেরিকার চিরশত্রু রাশিয়া তো তার চেয়ে প্রযুক্তির দিক থেকে কোনো অংশে কম নয়। এখন মনে হচ্ছে, প্রযুক্তিতে আমেরিকাকে রাশিয়া পরাস্ত করে ফেলেছে। আমেরিকার ক্ষমতায় কে আসবে, তার ইচ্ছারও একটি নমুনা দেখিয়ে দিয়েছে। তা না হলে ফলাফল উল্টে দেয়ার মতো এমন তথ্য কেন সিআইএ’র প্রতিবেদনে উঠে আসবে?
দুই.
প্রযুক্তির এ যুগে সাইবার হামলায় অনেক বড় বড় অঘটন ঘটিয়ে দেয়ার নজির ইতোমধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এক উইকিলিস যেভাবে একের পর এক বিশ্বের ক্ষমতাধর দেশ ও ব্যক্তির গোপন তথ্য প্রকাশ করে দিচ্ছে, তা সাইবার হামলা বা হ্যাকিং ছাড়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। আমাদের দেশে যে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে আটশ মিলিয়ন ডলার চুরি হয়ে গেছে, তা এই সাইবার হ্যাকিংয়ের মাধ্যমেই হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, প্রযুক্তির এ যুগে মানুষের যোগাযোগ ও কার্যক্রম যেমন গতি পেয়েছে, তেমনি চুরিচামারি এমনকি একজনের মানসম্মান নিয়ে খেলাধুলা করার ঘটনাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা নিউটনের তৃতীয় সূত্রের মতো অ্যাকশনের রিঅ্যাকশনÑ সেটা ভালো হোক আর মন্দ হোক। সাইবার হামলার মাধ্যমে ট্রাম্পের বিজয় হয়েছে কিনা, তা এখনই বলা মুশকিল। তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়ার পর তা স্পষ্ট হবে। তবে নির্বাচনে ট্রাম্প যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক, টুইটার, ওয়েবসাইটসহ অন্যান্য প্রযুক্তির ভালো ব্যবহার করেছেন এবং তা যে তার বিজয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, তা এখন প্রকাশিত হচ্ছে। ট্রাম্প নিজেও তা স্বীকার করেছেন। নির্বাচনে জেতার জন্য নীতি-নৈতিকতার ধার না ধরে ট্রাম্প যদি একে ‘যুদ্ধ’ হিসেবে নিয়ে থাকেন, তবে বলার কিছু নেই। কারণ ভালোবাসা ও যুদ্ধ নাকি কোনো নিয়মনীতির তোয়াক্কা করে না। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল ও নির্বাচনে জেতার জন্য ট্রাম্প যে ‘মিথ্যা’র আশ্রয় নিয়েছেন, তা নীতি-নৈতিকতার মধ্যে তো পড়েই না, গণতান্ত্রিক রীতিরও পরিপন্থী। এটা তার কৌশল হলেও বোধসম্পন্ন মানুষের কাছে তা চরম অপকৌশল হিসেবেই বিবেচিত হয়ে থাকবে। ‘মিথ্যা’ দিয়ে জয়লাভ করা ট্রাম্প আমেরিকানদেরও ‘লজ্জা’ হয়ে থাকবেন। নির্বাচনী প্রচারণার সময় সামাজিক যোগাযোগ ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ট্রাম্পের প্রচারক দল এমন কিছু ‘মিথ্যা’ তথ্য প্রচার করে, যা ভোটাররা বিশ্বাস করে এবং যারা তাকে ভোট দিতেন না তারাও তাকে ভোট দিয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ট্রাম্পের ‘মিথ্যা’ তথ্য প্রচারের নমুনাগুলোর মধ্যে রয়েছেÑ ‘পোপ ফ্রান্সিস প্রেসিডেন্ট পদে ট্রাম্পকে সমর্থন দিয়েছেন’, ‘হিলারির ই-মেইল কেলেঙ্কারি নিয়ে তদন্তে নিয়োজিত এফবিআই এজেন্ট খুন হয়েছেন’, ‘প্রেসিডেন্ট ওবামা ও হিলারি ক্লিনটন হাজার হাজার অবৈধ অভিবাসীকে বৈধতা দিতে সম্মত হয়েছেন’, ‘সিএনএন জানিয়েছে, ফ্লোরিডায় ভোটবুথ ফেরত ভোটারদের জরিপে অধিকাংশই ট্রাম্পের পক্ষে ভোট দিয়েছেন’, ‘যে হাজার হাজার মানুষ ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে অংশ নেয়, হিলারির ক্যাম্পেইন থেকে তাদের বাসে করে নিয়ে আসা হয়েছে’। বলা হচ্ছে, এসব মিথ্যা তথ্য ট্রাম্পের জয়ের ক্ষেত্রে বড় ধরনের ভূমিকা রেখেছে। কারণ ফেসবুক, টুইটার ও ওয়েবসাইটে এসব তথ্য পোস্ট করার পরপরই লাখ লাখ লোক তা বিশ্বাস করে এবং শেয়ার করা শুরু করে। পাঠক লক্ষ্য করুন, ট্রাম্পের প্রচারক দল যে তথ্যগুলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করে, সেগুলো খুবই স্পর্শকাতর। একজন ভোটারের মন ঘুরিয়ে দিতে যথেষ্ট। খ্রিস্টানদের কেউ যদি বিশ্বাস করে পোপ ফ্রান্সিস ট্রাম্পকে সমর্থন দিয়েছেন, তাহলে এ সমর্থন উপেক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ এ তথ্যটি পুরোপুরি মিথ্যা ছিল। দেখা যাচ্ছে, নির্বাচনী প্রচারণায় ট্রাম্প খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় আবেগ ও ধর্মকে বেশ ভালোভাবে ব্যবহার করেছেন। যদি বলা হয়, ভোটবুথ ফেরত বেশির ভাগ ভোটার ট্রাম্পকে ভোট দিয়েছেন, তাহলে সাধারণ ভোটাররা কখনই চাইবেন না, তার ভোটটি পরাজিত হতে যাওয়া প্রার্থীকে দিয়ে নষ্ট করতে। ট্রাম্পের প্রচারক দল ভোটারদের এই সাইকোলজি সূচারুরূপে কাজে লাগিয়েছে। তারপর যদি বলা হয়, ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমাবেশে হিলারির ক্যাম্পেইন থেকে বাসে করে লোক আনা হয়েছেÑ এ কথা শুনলে যে কোনো সচেতন ব্যক্তিই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠবেন। বিষয়টি এমন, একজন প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ জনগণকে উসকে দিচ্ছেÑ এটা কেমন কথা! ট্রাম্পের প্রচারণা দল এমন মিথ্যা তথ্য দিয়ে অনেক ভোটারের মধ্যে ক্ষুব্ধতা সৃষ্টি করে হিলারির সর্বনাশ করেছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, আমেরিকার ভোটাররা কি এতটাই নির্বোধ যে, এসব তথ্য বিশ্বাস করে ট্রাম্পকে ভোট দিয়ে দেবে? প্রশ্নের জবাবে বলা যায়, এক্ষেত্রে তারা নির্বোধ। কারণ তারা এমন ঢাহা মিথ্যা প্রচারণার মুখোমুখি কখনই হয়নি। এমন ‘ট্রু লাই’ বা সত্যিকারের মিথ্যা হতে পারে, তা তাদের ধারণার মধ্যেই ছিল না। তাদের রাজনীতি ও নির্বাচনী প্রচারণার ধরন এমন নয়। ফলে যখন এগুলো প্রচার করা হয়, সহজেই তারা বিশ্বাস করে। বাংলাদেশের মানুষ হলে এ ধরনের মিথ্যা তথ্য দ্বারা খুব একটা প্রভাবিত করা যেত না। কিছু মানুষ বিশ্বাস করলেও বেশির ভাগ মানুষ এসব ‘প্রচারণা’ তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিত। তারা ভালো করেই জানে, আমাদের নেতা-নেত্রীদের মুখের ভাষা কেমন। পরস্পরকে কী ভাষায়, কীভাবে ঘায়েল করে, তা তারা সুদীর্ঘকাল ধরে অবলোকন করে আসছে।
তিন.
ট্রাম্পের প্রচারণার কাজে নিয়োজিত দল মিথ্যা তথ্য প্রচারের এমন ধারণা পেয়েছে আমেরিকার একজন সাধারণ ব্যক্তির কাছ থেকে। এই লোক তার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে মিথ্যা খবর ছড়িয়ে মাসের পর মাস বেশ উপার্জন করে আসছে। বিষয়টি ট্রাম্পের পুত্র এরিকের নজরে আসে। তার আগে জেনে নেয়া যাক টুইটার, ফেসবুক, ওয়েবসাইট ও অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কীভাবে অর্থ উপার্জন করা যায়। ইন্টারনেটের ব্যবসায়িক নিয়ম অনুযায়ী কোনো তথ্য নির্দিষ্ট সংখ্যায় শেয়ার হলে তাতে বিজ্ঞাপন জুড়ে দেয়া হয় এবং সাইটের ওনার বা মালিক তা থেকে লভ্যাংশ পেয়ে থাকেন। যত বেশি শেয়ার হবে, তত বেশি লাভ। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে অংশ নিতে হিলারির পক্ষ থেকে বাস ভাড়া করে লোক নিয়ে আসা হয়েছেÑ এ মিথ্যা তথ্যটি টেক্সাসের মার্কেটিং কোম্পানির মালিক এরিক টাকারের নজরে আসে। তখন তার টুইটার অ্যাকাউন্টে ফলোয়ারের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪০ জন। তিনি যখন খবরটি তার টুইটারে শেয়ার করা শুরু করেন, তখন কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তা ১৬ হাজার বার শেয়ার হয় এবং তার ফেসবুকে শেয়ার হয় সাড়ে ৩ লাখ বার। এর মাধ্যমে এরিক টাকার ব্যাপক লাভবান হন। পল হর্নার নামে এক ব্যক্তি অনেক আগে থেকে ইন্টারনেটে তার ব্যবসা চালিয়ে আসছে। তার কাজই ছিল অসত্য ও চটকদার তথ্য দিয়ে শেয়ারের সংখ্যা বাড়িয়ে রোজগার করা। সে স্বীকার করেছে, ফেসবুকে মিথ্যা খবর দিয়ে মাসে কম করে হলেও ১০ হাজার ডলার উপার্জন করে। এভাবে আরও অনেকে মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করে সে উপার্জন করে চলেছে। ট্রাম্পের প্রচারক দল উক্ত ব্যক্তিদের এ কৌশল নির্বাচনী প্রচারণায় কাজে লাগায়। তারা উল্লিখিত মিথ্যা তথ্য প্রচার করে ভোটারদের প্রভাবিত করে বিজয় ছিনিয়ে আনে। বিষয়টি এমন হয়ে দাঁড়ায়, কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ। তথ্য প্রযুক্তির কারণে ক্ষমতার মসনদ যেমন উল্টে যায়, তেমনি নিশ্চিত ক্ষমতাসীন ব্যক্তিকেও পরাজয়ের গ্লানি মেখে দেয়। এখন প্রশ্ন উঠেছে, ট্রাম্পের এ নির্বাচনী প্রচারণায় মিথ্যা তথ্যের আশ্রয় না নিলে কি হিলারি জয়ী হতেন? জবাবে বলা যায়, হলেও হতে পারতেন। কারণ জরিপগুলো বরাবরই বলছিল, হিলারি অবশ্যম্ভাবীভাবে বিজয়ী হতে চলেছেন। নির্বাচনের দিন দুপুরেই যখন নিশ্চিত হয়ে যায়, হিলারি হেরে যাচ্ছেন, তখন তা গোটা আমেরিকা তো বটেই, সারা বিশ্ব ‘স্তম্ভিত’ হয়ে যায়। কী থেকে কী হয়ে গেল, কেমন করে হচ্ছে, বিশ্বজুড়ে এমন মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। বিশ্লেষকরা চুলচেরা বিশ্লেষণ করে নানা যুক্তি দাঁড় করাতে চেষ্টা করেন। তবে এটা এখন অনুমিত হচ্ছে, ট্রাম্পের মিথ্যা তথ্যের প্রচারণা নীরবে ভোটের ফলাফল পরিবর্তন করে দিয়েছে। এর সাথে সাইবার হামলা তো রয়েছেই। অর্থাৎ ডিজিটাল প্রযুক্তির অপব্যবহার যে কত মারাত্মক ফলাফল বয়ে আনতে পারে, এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে থাকবে এবারের আমেরিকার নির্বাচন। ভবিষ্যতে হয়তো উইকিলিস বা উইকিলিসের মতো আরও আধুনিক কোনো প্রযুক্তি প্রকাশ করে দেবে ট্রাম্পের বিজয়ের অবিস্মরণীয় কাহিনী। প্রযুক্তি যে কতটা শক্তিশালী হতে পারে এবং ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে, তার প্রথম নজির দেখা যায়, ১৯৮৯ সালে চীনের বেইজিংয়ে তিয়েনআনমেন স্কয়ারে ছাত্রদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সময়। তখন ফেসবুক, টুইটারের মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ছিল না। ছাত্ররা মোবাইলে এক ধরনের সঙ্কেত বা মেসেজের মাধ্যমে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে এই স্কয়ারে জড়ো হয়। পুরো তিয়েনআনমেন পরিণত হয় জনসমুদ্রে। সে সময়ের সরকার ‘মার্শাল ল’ জারি করে গণহত্যা না চালালে চীনের ইতিহাসই বদলে যেত। তা হয়নি সরকারের কঠোর পদক্ষেপের কারণে। তবে তিয়েনআনমেনের ছাত্র আন্দোলন এখনো ইতিহাস হয়ে রয়েছে। প্রযুক্তির এ যুগে জরিপ যে এখন অনেকটাই অকার্যকর, তা ট্রাম্পের নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে পরিষ্কার হয়ে গেছে। বলা হতো, আমেরিকার নির্বাচনে জরিপের ফলাফল খুব কমই বিফল হয়। এবার দেখা গেল, তার পুরোটাই ব্যর্থ হয়েছে। এর কারণ প্রযুক্তি, বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সত্য-অসত্য ও বিচিত্র তথ্যের ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে মানুষের মনোভাবকে প্রভাবিত করার নিপুণ ও বিপুল ক্ষমতা। এর ক্ষমতা এতটাই যে, নিশ্চিত ভোটকেও মুহূর্তে পরিবর্তন করে ফেলতে পারে। ট্রাম্প যে নির্বাচিত হলেন, তা জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে নয়, বলা যায় তথ্য-প্রযুক্তির নীরব বিপ্লবের মাধ্যমে। সেটা যতই মিথ্যা ও অনৈতিক হোক। বিজয় তো নিশ্চিত করা গেছে। কাজেই এখন বোধ হয়, জরিপের ওপর নির্ভর করার দিন শেষ হয়ে আসছে। আমাদের দেশে জরিপের নির্ভরযোগ্যতা এবং এর প্রতিফলন খুব কম হয়। তারপরও মাঝে মাঝে বিভিন্ন ইস্যুতে জরিপ করতে দেখা যায়। কিছু সংখ্যক মানুষের বয়স, শ্রেণী, শিক্ষা এবং নির্দিষ্ট এলাকার ভিত্তিতে সাধারণত জরিপ করা হয়। এসব জরিপ যার পক্ষে যায়, তারা উৎফুল্ল হয়, বিপক্ষে গেলে প্রতিবাদমুখর হয়। সম্প্রতি ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল নামে একটি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষমতায় যাওয়া নিয়ে একটি জরিপ করে। এতে দেখানো হয়, এ মুহূর্তে জাতীয় নির্বাচন হলে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ পাবে শতকরা ৩৮ ভাগ ভোট, বিএনপি পাবে ৫ ভাগ, জাতীয় পার্টি ১ ভাগ ও জামায়াতে ইসলামী পাবে ২ ভাগ। এ জরিপে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ খুবই খুশি। অন্যদিকে বিএনপি তা প্রত্যাখ্যান করেছে। সরকারের শরিক জাতীয় পার্টি বারবার আগামীতে তারাই ক্ষমতায় যাবে বলে মুখে ফেনা তুলে ফেললেও এর কোনো প্রতিবাদ করেনি। অথচ ২০১৪ সালে এই ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনালের জরিপেই উল্লেখ করা হয়েছিল, সে সময় নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগ পাবে ৩৮ শতাংশ, বিএনপি পাবে ৩৫ শতাংশ। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এ সময়ে সংস্থাটি যে জরিপ করেছে, তাতে আওয়ামী লীগের ভোটের হার কমেনি, একই রয়েছে। বিএনপির ৩০ শতাংশ ভোট কমে গেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, বিএনপির এই ৩০ শতাংশ ভোটার গেল কোথায়? আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য প্রধান দলে গেলে তো তাদের হার অনেকটা আকাশচুম্বী হয়ে যাওয়ার কথা! তা তো হয়নি। আবার এটাও হতে পারে, বিএনপির এই বিপুলসংখ্যক ভোটার নিশ্চুপ হয়ে গেছে। আর নিশ্চুপ হয়ে যাওয়ার মানে কি এই ভোট দেয়ার সুযোগ পেলে তারা বিএনপিকে ভোট দেবে না? এটা কি হয়? সাধারণ হিসেবেই তো ধরা হয়, আওয়ামী লীগ ও বিএনপির ভোটের হার উনিশ-বিশের মতো। বিএনপি বা আওয়ামী লীগের এই ভোটের হার কি একেবারে তলানিতে ঠেকিয়ে দেয়া সম্ভব? সম্ভব নয়। আমরা দেখেছি, ২০০৮ সালের নির্বাচনে বিএনপি সংসদে ৩০-৩২টি সিট পেলেও তার ভোটের হার ছিল ৩০-এর উপরে। কাজেই এসব জরিপ যে আমাদের দেশের জন্য খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, তা অতীতের নজির থেকেই বোঝা যায়। আর যেখানে আমেরিকারই প্রতিষ্ঠান ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল জরিপ করেছে, তা এখন বিশ্বাস করা তো খুবই কঠিন। কারণ তার এ বছরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেই তো বাঘা বাঘা সংবাদ মাধ্যম ও প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের অব্যর্থ জরিপগুলো মুখ থুবড়ে পড়েছে। কাজেই প্রযুক্তির এ যুগে কিছু লোকের সাথে কথা বলে জরিপের ফলাফলের বিষয়টি অকার্যকর হয়ে গেছে। বরং কে পাস করবে আর কে হারবে এটা সবসময় নির্ভর করে কে কত বেশি ভোটারের কাছে পৌঁছতে পারে, তার ওপর। আর এখন প্রযুক্তির যুগে ভোটারের কাছে সহজে পৌঁছানোর মাধ্যমই হচ্ছে ফেসবুক, টুইটার, ওয়েবসাইটসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। এটা এখন এতটাই শক্তিশালী যে আমেরিকার মতো নির্বাচনী ফলাফল উল্টে দেয়ার ক্ষমতা রাখে। এমনকি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বা সরকার প্রধানরা জাতিকে কোনো মেসেজ বা দিকনির্দেশনা দিতে চান, তারাও এখন টুইটারের আশ্রয় নিচ্ছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রায়ই টুইট করে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন। বাংলাদেশেও সম্ভবত কোনো রাজনৈতিক দলের প্রধান হিসেবে বেগম খালেদা জিয়া প্রথমবারের মতো এই ‘টুইট’ করা শুরু করেছেন। এর ফলে অতি দ্রুত তার কথা সংবাদ মাধ্যম থেকে শুরু করে ব্যাপক সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে।
চার.
বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচনে প্রচার-প্রচারণার ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে। নিজ নিজ দল বা জোটের প্রচারণা নিয়ে যদি অনেকটা ‘সাইবার যুদ্ধ’ লেগে যায়, তাতে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। এর নমুনা রাস্তাঘাটে চলাচল করতে গেলেই বোঝা যায়। হাঁটতে, চলতে, ফিরতে কিংবা বসে থেকেও মানুষ মোবাইলে নিজ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সর্বক্ষণ দৃষ্টি রেখেই চলেছে। প্রতি মুহূর্তে কী আপডেট আসছে, তা জানার আগ্রহ তাদের মধ্যে প্রবল। মোবাইল ব্যবহারকারী দশ কোটি মানুষের মধ্যে যদি পাঁচ কোটিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে থাকে, তবে নির্বাচনী প্রচারণা থেকে শুরু করে যে কোনো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু চোখের পলকে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়া অসম্ভব কিছু নয়। ফলে আগামী জাতীয় নির্বাচনে যে প্রযুক্তির এ মাধ্যম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে, তাতে সন্দেহ নেই। তবে এর দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহারটির ওপর জোর দিতে হবে। আমরা দেখেছি, মিথ্যা সংবাদ ছড়িয়ে কী তুলকালাম কা-ই না ঘটে গেছে। স্বাভাবিকভাবেই আশা করব, রাজনৈতিক দলগুলো তাদের ইতিবাচক বক্তব্য ও কর্মকা- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তুলে ধরে মানুষকে প্রভাবিত ও দিকনির্দেশনা দেবে। রাজনৈতিক দলগুলোর ইতিবাচক কথাবার্তা ও তথ্য দেয়ার মধ্য দিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেকের আয়-রোজগারের পথও প্রশস্ত করতে সহায়তা করবে। পাশাপাশি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সত্যকে মিথ্যা বা মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করার অপপ্রয়াস অবশ্যই বর্জন করতে হবে।
[email protected]

![]() দৈনিক ইনকিলাব সংবিধান ও জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাই ধর্ম ও রাষ্ট্রবিরোধী এবং উষ্কানীমূলক কোনো বক্তব্য না করার জন্য পাঠকদের অনুরোধ করা হলো। কর্তৃপক্ষ যেকোনো ধরণের আপত্তিকর মন্তব্য মডারেশনের ক্ষমতা রাখেন।
দৈনিক ইনকিলাব সংবিধান ও জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাই ধর্ম ও রাষ্ট্রবিরোধী এবং উষ্কানীমূলক কোনো বক্তব্য না করার জন্য পাঠকদের অনুরোধ করা হলো। কর্তৃপক্ষ যেকোনো ধরণের আপত্তিকর মন্তব্য মডারেশনের ক্ষমতা রাখেন।