হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির খড়গ : আসামের এনআরসি এবং বাংলাদেশ
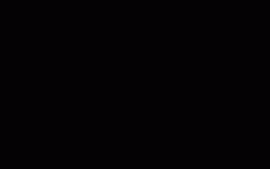
কিশোর শিক্ষার্থীদের নিরাপদ সড়ক দাবীর আন্দোলনে ঢাকাসহ সারাদেশে তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা ও অনিশ্চয়তা দেখা যাচ্ছিল,
জামালউদ্দিন বারী : পদ্মার বিশাল অংশ শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেছে। অধিকাংশ এর শাখা নদী ইতোমধ্যেই অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে। গত চার দশকে দেশের নৌপথের দৈর্ঘ্য দশ ভাগের একভাগে নেমে এসেছে। উত্তরঞ্চলের অন্যতম বড় নদী তিস্তা অববাহিকার কয়েক কোটি মানুষ এখন পানির জন্য হাহাকার করছে। দেশের অন্যতম বৃহৎ তিস্তা সেচ প্রকল্প পানির অভাবে মুখ থুবড়ে পড়েছে। নদীতে পানি না থাকায় সেচ প্রকল্পগুলো ভূগর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় পানির স্তর দ্রুত সেচ পাম্পের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। এর সাথে যুক্ত হচ্ছে আর্সেনিক সমস্যা ভ‚গর্ভে পানি ও মাটির স্তরের মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ভূমিকম্প এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশঙ্কা ক্রমে বেড়ে চলেছে। গত এক দশকে নদ-নদীর নাব্য হারানো ও পানির সমস্যা জনমানুষের জীবনযাত্রায় সংকট সৃষ্টি করেছে এবং আগামী দিনে এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়কে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে। অথচ দেশের শাসক শ্রেণিকে এসব বিষয়ে নিস্পৃহ এবং নিঃশঙ্ক দেখা যাচ্ছে। বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলোতে মাত্রাতিরিক্ত ফসিল জ্বালানি ব্যবহারের কারণে তথাকথিত উন্নয়ন ও শিল্পায়নের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবে জলবায়ু ও আবহাওয়ার পরিবর্তনের ছোবলে দেশে দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মানবিক বিপর্যয় যখন অনিবার্য হয়ে উঠেছে, ঠিক তখনই বিশ্বের উন্নয়ন পরিকল্পনাবিদরা গতানুগতিক উন্নয়নের স্থলে টেকসই উন্নয়নের রূপরেখা মেলে ধরতে শুরু করেছেন। ইতোমধ্যেই আমাদের এই সবুজ গ্রহের অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশে গত ১০ হাজার বছরে বিশ্বের ইকোলজির যত ক্ষতি হয়েছে, শিল্পায়ন ও বাণিজ্যিক উন্নয়নে এগিয়ে থাকার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে গত দেড়শ বছরে ধরিত্রীর ক্ষতির পরিমাণ তার চেয়ে বহুগুণ বেশি। ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্তির চিরন্তন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সংগ্রামকে কর্পোরেট মুনাফাবাজদের হাতে ছেড়ে দিয়ে বিশ্বের জন্য এই বিপর্যয়কে ত্বরান্বিত ও অনিবার্য করে তোলা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় গঠিত আন্তর্জাতিক ফোরাম ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো ক্লাইমেট চেঞ্জ ও জলবায়ু উদ্বাস্তু কবলিত দেশগুলোর তালিকায় বাংলাদেশকে অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে গণ্য করছে। এ হিসেবে ক্লাইমেট মিটিগেশনের এসব ফোরামে বাংলাদেশ তার অবস্থানকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে ক্লাইমেট ফান্ড থেকে তার ন্যায্য পাওনা বুঝে নিতে চায়। তবে শুরু থেকে এখন পর্যন্ত আমাদের সরকার এ ক্ষেত্রে তাদের ধারাবাহিক ব্যর্থতার ধারাই শুধু অব্যাহত রেখেছে। দুর্নীতি-অব্যবস্থাপনা ও অস্বচ্ছতার অভিযোগ তুলে বাংলাদেশকে ক্লাইমেট ফান্ডের পাওনা বুঝিয়ে দিতে তালবাহানা করছে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো।
শাসকশ্রেণি যদি রাষ্ট্র ও জনগণের অগ্রাধিকার ও টেকসই উন্নয়নের বিষয়গুলো নির্ধারণে ব্যর্থ হয়, তাহলে দ্রুত একসময় রাষ্ট্রের ভঙ্গুরতা, জনদুর্ভোগ ও বিপর্যয় অনিবার্য রূপ লাভ করে। এই মুহূর্তে আমাদের রাষ্ট্রের অগ্রাধিকার কী তা একজন সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনার মানুষও বোঝে। প্রথমত, সামাজিক-রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, জননিরাপত্তা ও সুশাসন, দ্বিতীয়ত পরিবেশগত বিপর্যয় থেকে দেশকে রক্ষা, খাদ্য নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রশ্নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ। এসব বিষয়কে অগ্রাহ্য করেই তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলো এখনো তথাকথিত উন্নয়নের শ্লোগান তুলে জনগণের রাজস্বের হাজার হাজার কোটি টাকার তহবিল কর্পোরেট মুনাফাবাজি, লুটপাট ও কমিশন বাণিজ্যের ভাগাভাগিতে বরাদ্দ করছে। বিশেষত অবকাঠামোগত মেগা প্রকল্প গ্রহণের সাথে যতটা না টেকসই উন্নয়ন ও জনগণের স্বার্থের বিষয় থাকে, তার চেয়ে শাসকশ্রেণি, মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরাশক্তি গুলোর রাজনৈতিক কৌশলগত ও অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত থাকে। আজ যখন নদীগুলো পানিশূন্য হয়ে পড়েছে, দেশের সেচ প্রকল্পগুলো বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে তখন আমাদের সরকার, সকল রাজনৈতিক দল ও রাষ্ট্রশক্তির অগ্রাধিকার ও প্রধান বিবেচ্য বিষয় হওয়ার কথা আমাদের নদীগুলোর পানি প্রবাহ ঠিক রাখার যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা। কিন্তু সরকার পদ্মা নদীর অস্তিত্ব রক্ষার চেয়ে পদ্মা নদীর ওপর ব্রিজ নির্মাণের প্রকল্পকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে তা বাস্তবায়ন করছে। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, পদ্মার ওপর ব্রিজ নির্মিত হলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের জন্য ঢাকাসহ দেশের বাকি অংশের সাথে যোগাযোগ অনেক সহজ হবে। সড়ক ও রেল যোগাযোগের এই উন্নয়ন দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও সুষম উন্নয়নেও ইতিবাচক অবদান রাখবে। তবে পদ্মা নদীর অস্তিত্বের চেয়ে নিশ্চয়ই পদ্মা ব্রিজ বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। পুঁজিবাদী দুর্নীতিগ্রস্ত অর্থনীতির দেশগুলোতে রাষ্ট্রশক্তি, মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন এবং বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো পারস্পরিক স্বার্থ ও বোঝাপড়ার মধ্য দিয়েই তথাকথিত উন্নয়ন প্রকল্পে অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব গ্রহণ করে থাকে। কখনো কখনো তাদের মধ্যে মতপার্থক্য ও স্বার্থের দ্ব›দ্বও প্রবল হয়ে ওঠে। সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের পদ্মা সেতু প্রকল্প তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে উঠেছে। পদ্মা সেতু প্রকল্প শুরুর আগেই বিশ্বব্যাংক সরকারের সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির যোগসাজশের অভিযোগ এনে এ প্রকল্পে প্রায় দেড় বিলিয়ন ডলার অর্থায়নের চুক্তি থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেয়। পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকেও বিশেষ ব্যক্তি ও মহলের প্রভাবে বিশ্বব্যাংকের পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তোলা হয়। কানাডার একটি কোম্পানি এসএনসি নাভালিনের কয়েকজন কর্মকর্তাসহ পদ্মা সেতু প্রকল্পে কথিত দুর্নীতির অভিযোগ কানাডার আদালতে প্রমাণিত না হওয়ার খবরটি প্রকাশিত হওয়ার পর সরকারের সংশ্লিষ্টরা তাদের গলার স্বর বহুগুণ চড়িয়ে দিয়ে বিশ্বব্যাংক, প্রফেসর ইউনূস এবং সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটনের বিরুদ্ধে নতুন নতুন অভিযোগের ফর্দ তুলে ধরছেন। অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের মাত্রা ও ভিত্তি যাই হোক, আমাদের মেগা উন্নয়ন প্রকল্পের নামে সরকার, বিশ্বব্যাংক, পরাশক্তিসহ নেপথ্যের কুশীলবদের ভ‚মিকা ও স্বার্থদ্ব›দ্ব এসব থেকে অনেকটা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। জাতিসংঘসহ বিশ্বসংস্থাগুলো এমডিজি ও এসডিজি বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে বড় বড় সম্মেলন করলেও আমাদের মতো দেশের অস্তিত্বের সাথে জড়িত পদ্মা-তিস্তার প্রবাহ ঠিক রেখে নদী অববাহিকার কোটি কোটি মানুষের জীবন-জীবিকার নিশ্চয়তা অর্গলমুক্ত করার বদলে মারণাস্ত্র প্রকল্পের চেয়েও ভয়াবহ ফারাক্কা ব্যারাজ, তিস্তার উজানে গজলডোবা ব্যারাজ অথবা পদ্মা সেতু প্রকল্প নিয়ে অতি উৎসাহী ও রশি টানাটানিতে ব্যস্ত হতে দেখা গেছে। মূলত সব পক্ষই সাময়িক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক লাভালাভের কথা বিবেচনা করে রাষ্ট্র ও জনপদের ভবিষ্যৎ অনিবার্য বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।
আজ থেকে শত বছর আগে ব্রিটিশ সরকার প্রথম পদ্মার ওপর পৌনে দুই কিলোমিটার দীর্ঘ ইস্পাতের রেল সেতু (হার্ডিঞ্জ ব্রিজ) নির্মাণ করেছিল। সে সময় হার্ডিঞ্জ ব্রিজের নিচ দিয়ে বড় বড় স্টিমার চলাচল করত। সেই পদ্মা এখন ‘আমাদের ছোট নদী’-তে পরিণত হয়েছে। হার্ডিঞ্জ ব্রিজের নিচ দিয়ে এখন মানুষ-গরু ও গাড়ি অনায়াসে পার হতে পারে। যমুনার ওপর সেতু নির্মিত হওয়ার এক দশকের মধ্যেই অসংখ্য চর পড়ে যমুনা নদীর নাব্য হারাতে শুরু করেছে। এটা ঘটেছে যতটা না নদী শাসনের কারণে তার চেয়ে বেশি উজানে ভারতের বাঁধ নির্মাণ ও পানি প্রত্যাহারের কারণে। নদীর ওপর বড় বড় বাঁধ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের মেগা প্রকল্প কোনো একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষকে সাময়িক সুবিধা দিলেও এক সময় এসব প্রকল্প পুরো অঞ্চলের পরিবেশগত ভারসাম্যের জন্য বিষফোঁড়া হয়ে দেখা। মার্কিন সরকার সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এ ধরনের প্রায় ৫০০ বাঁধ ডিকমিশন্ড বা অপসারণ করেছে বলে জানা যায়। যে লক্ষ্যে ভারত সরকার এক সময় ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করেছিল, কার্যত কখনো সে লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। চালু করার চার দশকের মধ্যেই ফারাক্কার ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাব ভারত ও বাংলাদেশে চরম আকার ধারণ করেছে। একদিকে হুগলি-ভাগিরথি মোহনায় পলি জমে ভরাট হয়ে যাওয়া, সাংবাৎসরিক বন্যা, নদীভাঙন, অন্যদিকে বাংলাদেশের পদ্মা-মেঘনায় বড় বড় চর জেগে নাব্য হারিয়ে পদ্মা-মেঘনার শত শত শাখা নদী বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ফারাক্কা প্রকল্প নিয়ে প্রাথমিক সমীক্ষা বা ফিজিবিলিটি রিপোর্ট গ্রহণের সময়ই এমন পরিবেশগত বিপর্যয়ের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও প্রকৌশলীরা। এ কারণে শত বছর আগেই ব্রিটিশ সরকার ফারাক্কা বাঁধ নিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও তারা তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়নি। উপনিবেশোত্তর ভারতে ফারাক্কা বাংলাদেশের জন্য মরণ ফাঁদ হিসেবে কার্যকর প্রমাণিত হওয়ার পর তিস্তার উজানে গজলডোবা বাঁধ নির্মাণ তিস্তার মরণদশা নিশ্চিত করা হয়েছে। এরপর এখন টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে এক ধরনের লুকোচুরি খেলা চলছে। এমনকি ৫৪টি অভিন্ন নদীর পানি প্রত্যাহারের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে তিলে তিলে ঊষর মরুভ‚মিতে পরিণত করার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। তথাকথিত মেগা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের চেয়ে এই ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করা বাংলাদেশের জন্য অনেক বড় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু।
এখনকার রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারক ও পরিকল্পনাবিদরা প্রায়শ সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট এবং গ্রিন ইকোনমির কথা বললেও বাস্তবে তারা জাতিকে বিপরীত দিকেই হাঁটাচ্ছেন। গত দুই দশকে সুন্দরবনের আশপাশে শত শত ভারী শিল্পের অনুমোদন দিয়ে, সুন্দরবনের স্পর্শকাতর এলাকায় বাণিজ্যিক নৌ চ্যানেল চালু রেখে এবং কোটি মানুষের প্রতিবাদ ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার উদ্বেগ-আশঙ্কা অগ্রাহ্য করে সুন্দরবনের কাছে রামপালে দেশের বৃহত্তম কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের ধনুর্ভঙ্গ পণ করে সরকার জনগণের কাছে কী বার্তা দিচ্ছে? এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, সরকার জনস্বার্থেই কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের পদক্ষেপ নিচ্ছে। তবে বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং বিদ্যুতের অনেক বিকল্প থাকলেও বাংলাদেশের জন্য সুন্দরবনের কোনো বিকল্প নেই। এ ক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞ মতামত, পরিবেশবাদীদের উদ্বেগ এবং সরকারের পক্ষ থেকে পাল্টা যুক্তি ও আল্ট্রা ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তির দোহাই ইত্যাদি বিষয়গুলো বাদ দিলেও প্রতিদিন হাজার টন কয়লার জোগান নিশ্চিত করতে সুন্দরবনের নৌ চ্যানেল দিয়ে প্রতি মাসে শত শত লাইটারেজ জাহাজ চলাচলের বিপর্যয়কর দিকটি ইতোমধ্যে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়েছে। দুই বছর আগে ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে সুন্দরবনের শ্যালা নদীতে তেলবাহী ট্যাঙ্কার ডুবে সাড়ে তিন লাখ লিটার তেল সুন্দরবনের খাল ও জলাভ‚মিতে ছড়িয়ে পড়লে মারাত্মক পরিবেশগত বিপর্যয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিরল প্রজাতির ইরাবতি ডলফিন, মাছসহ অসংখ্য জলজ প্রাণী প্রজাতির অস্তিত্বসংকট দেখা দেয়। রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রে যতই সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি ব্যবহার করা হোক, এসব প্রযুক্তি এমন দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কোনো কাজে আসবে না। শ্যালা নদীতে অয়েল ট্যাঙ্কার ডুবির ঘটনা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ হিসেবে প্রচার হয়, সুন্দরবন রক্ষায় সরকারের প্রতি ইউনেস্কোসহ সারা বিশ্বের পরিবেশবাদীদের উদ্বেগ ও সুপারিশমালা পাঠানো হয়। এরপর কিছু দিনের জন্য সুন্দরবনের কয়েকটি নৌ চ্যানেলে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল ও মাছ ধরা বন্ধ থাকলেও তা বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। এরপর থেকে আবারো কয়লা ও কেমিক্যালবাহী অনেকগুলো জাহাজ ডুবির ঘটনা ঘটেছে। রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের কারণে সুন্দরবনের যেসব ক্ষতির আশঙ্কার কথা বলা হচ্ছে তা পরিস্ফুট হতে হয়তো কয়েক দশক সময় লাগবে। তার আগে কোটি কোটি টন কয়লা পুড়িয়ে উৎপাদিত বিদ্যুতে বাংলাদেশে শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি আরো বেগবান হবে। দেশ লোডশেডিংমুক্ত হলে, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাতা-সমর্থকরা হয়তো রাজনৈতিক সমাবেশে বিজয়ীর বেশে বলবে, এটা আমাদের সাহসী উদ্যোগের ফসল। ওরা ঠেকাতে পারেনি। বছরের পর বছর ধরে লাখ লাখ টন জীবাশ্ম জ্বালানি বর্জ্য এবং বুড়িগঙ্গা-শীতলক্ষ্যার মতো সুন্দরবন নৌ চ্যানেল মারাত্মক দূষণের শিকার হওয়ার পর একদিন যখন সুন্দরবনের মৃত্যুঘণ্টা বাজবে তখন হয়তো আজকের রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের পক্ষ-বিপক্ষের কাউকেই খুঁজে পাওয়া যাবে না।
গত এক দশকে বিশ্বের দেশগুলোতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় দুটি পারস্পরিক সাংঘর্ষিক বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়েছে। গতানুগতিক ধারার পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধারণার পাশাপাশি ‘গ্রিন ইকোনমি’ নতুন প্রস্তাবনা হিসেবে উঠে এসেছে। এ প্রস্তাবনা তথাকথিত উন্নয়নের গতিকে শ্লথ করে দেয়ার পাশাপাশি এ ধরনের উন্নয়নের কোনো শর্টকাট রাস্তা না থাকায় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে ‘গ্রিড ইকোনমি’ বেশি গ্রহণীয় হয়েছে। জনগণের ওপর অতিরিক্ত কর ও ঋণের বোঝা এবং পরিবেশগত বিপর্যয়ের ঝুঁকি নিয়ে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সাথে বহুজাতিক কোম্পানি ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক ও রাজনৈতিক স্বার্থের বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভ‚মিকা রাখছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দুটি গুরুত্বপূর্ণ মেগা প্রকল্প পদ্মা সেতু এবং রামপাল কয়লাবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের ক্ষেত্রে দুই পরস্পর বৈরী শক্তি চীন ও ভারত ভিন্নতর অবস্থান গ্রহণ করেছে। বিতর্কিত অভিযোগে বিশ্বব্যাংক সরে দাঁড়ালেও নিজস্ব অর্থায়ন এবং রেলসংযোগসহ বর্ধিত কলেবরের পদ্মা সেতু প্রকল্পে জি টু জি ভিত্তিতে চীনা অর্থায়ন বাংলাদেশের মর্যাদা বাড়িয়েছে। তবে প্রকল্প ব্যয় তিন দফায় তিনগুণ বেড়ে যাওয়া ভিন্নতর আলোচ্য বিষয়। অন্যদিকে সুন্দরবনের ভারতীয় অংশে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের অনুরূপ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের প্রকল্প ভারতের পরিবেশ অধিদফতর এবং সরকার অনুমোদন না দিলেও বাংলাদেশের প্রায় সকল রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের যৌক্তিক বিরোধিতা উপেক্ষা করেই তারা সুন্দরবনের বাংলাদেশ অংশে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ অব্যাহত রেখেছে। অথচ প্রায় তিন দশক আগে বিশ্বব্যাংকের ঋণ সহায়তায় নর্মদা ব্যারাজ নির্মাণ চুক্তি ও প্রজেক্ট চ‚ড়ান্ত হওয়ার পরও নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের কাছে নতিস্বীকার করে বিশ্বব্যাংক নর্মদা প্রকল্প থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয় এবং ভারত সরকারও প্রকারান্তরে নর্মদা প্রকল্প বাস্তবায়ন থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয়। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, জনমত, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, পরিবেশগত বিবেচনার প্রশ্নে ভারত-বাংলাদেশের সরকার ও নীতিনির্ধারকদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। এমনকি ভারত সরকারের নীতিও নিজ দেশে ও বাংলাদেশে অভিন্ন নয়। সুন্দরবনের বাংলাদেশ অংশে রয়েল বেঙ্গল টাইগারসহ নানা ধরনের প্রাণী প্রজাতির হ্রাস ও বিলুপ্তি ঘটলেও ভারতীয় অংশে তা বাড়ছে। বিশ্বের অন্যতম ন্যাচারাল ট্রেজার এবং ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সুন্দরবনের বাংলাদেশ অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা বাদ পড়লে ভারত তার একক দাবিদার হতে পারে বলে কেউ কেউ মনে করছে। বর্তমান সরকার যখন পদ্মা সেতু নির্মাণের মাধ্যমে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের শত বছরের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দিতে যাচ্ছে, তখন শুধু দেশের দক্ষিণাঞ্চল নয়, পুরো বাংলাদেশের নিরবচ্ছিন্ন ও বিকল্পহীন সম্পদ ও প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুন্দরবনের নিরাপত্তা নিয়ে এমন অনাবশ্যক চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি নিচ্ছে কেন? যেখানে আগামী দশক নাগাদ সরকার ২৪ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছে, সেখানে রামপাল প্রকল্প পুনর্বিবেচনা ও নতুনভাবে চিন্তা করার অবকাশ রাখতে হবে। বিগত শতকে শিল্পোন্নত বিশ্বের অপরিকল্পিত শিল্পায়ন ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের খেসারত দিচ্ছে এখন বিশ্বের সব মানুষ। বিদ্যুতের হাজারটা বিকল্প থাকা সত্তে¡ও শ্রেফ জেদের বশে দীর্ঘমেয়াদে সুন্দরবন ধ্বংসের বা ক্ষতির আশংঙ্কা দৃঢ়তার সাথে পরিত্যাগ করতে হবে। গ্রীড ইকোনমির ধ্বংসাত্মক পরিনতি আমরা দেখছি- এখন সময় গ্রীন ইকোনমিতে অভ্যস্থ হওয়ার। নদী, বন ও পরিবেশগত উন্নয়নের শতবর্ষী পরিকল্পনা নিতে হবে।
[email protected]

![]() দৈনিক ইনকিলাব সংবিধান ও জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাই ধর্ম ও রাষ্ট্রবিরোধী এবং উষ্কানীমূলক কোনো বক্তব্য না করার জন্য পাঠকদের অনুরোধ করা হলো। কর্তৃপক্ষ যেকোনো ধরণের আপত্তিকর মন্তব্য মডারেশনের ক্ষমতা রাখেন।
দৈনিক ইনকিলাব সংবিধান ও জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাই ধর্ম ও রাষ্ট্রবিরোধী এবং উষ্কানীমূলক কোনো বক্তব্য না করার জন্য পাঠকদের অনুরোধ করা হলো। কর্তৃপক্ষ যেকোনো ধরণের আপত্তিকর মন্তব্য মডারেশনের ক্ষমতা রাখেন।