হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির খড়গ : আসামের এনআরসি এবং বাংলাদেশ
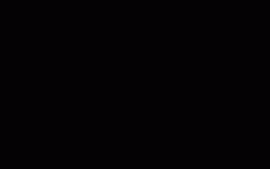
কিশোর শিক্ষার্থীদের নিরাপদ সড়ক দাবীর আন্দোলনে ঢাকাসহ সারাদেশে তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা ও অনিশ্চয়তা দেখা যাচ্ছিল,
মোহাম্মদ আবদুল গফুর : আমাদের দেশে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের মাস হিসেবে পরিচিত। ফেব্রুয়ারি এলেই আমরা সকলে যেন রাতারাতি বাংলা ভাষার ভক্ত হয়ে উঠি। যারা ইংরেজি মিডিয়ামের বিদ্যালয়ের ভক্ত তারাও শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যারা বুকের তাজা রক্ত দিয়ে শহীদ হয়েছেন তাদের প্রতি আনুষ্ঠানিক শ্রদ্ধা জানাতে ভুল করেন না। আন্তরিকতাহীন এসব আনুষ্ঠানিকতার কারণেই সম্ভবত ভাষা আন্দোলনের এত বছর পরেও ভাষা শহীদদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে পারছে না।
কিছু দিন আগে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিংহা বিচারকরা ভবিষ্যতে বাংলায় রায় লিখবেন বলে যে সুসংবাদ দিয়েছেন তার মধ্যেই কিন্তু একটি দুঃসংবাদও লুক্কায়িত রয়েছে। সেটি এই যে, ভাষা আন্দোলনের এত বছর পরও অনেক বিচারকই বিচারের রায় বাংলায় লিখছেন না। এ অভিযোগ শুধু বিচারকদের বিচারের রায় লেখা সম্বন্ধেই নয়, এরকমের অভিযোগ রয়েছে বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তাদের অফিসিয়াল নোট লেখা সম্বন্ধেও। এ অভিযোগ রয়েছে উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষাদানের মাধ্যম সম্বন্ধেও।
ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে আমাদের উদাসীনতা এতটাই গভীর ও ব্যাপক যে, ভাষা আন্দোলন কবে কীভাবে কোন পটভূমিতে শুরু হয়, সে ইতিহাসটা পর্যন্ত আমরা অনেকে জানার গুরুত্ব অনুভব করি না। অথচ এ ইতিহাস জানা আমাদের আজকের প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাস জানার স্বার্থেই অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসকে বলা হয়ে থাকে জাতির দর্পণ। আয়নায় যেমন আমরা আমাদের চেহারা দেখে থাকি, ইতিহাসের দর্পণে আমাদের জাতির অতীতের উত্থান-পতনের তথ্যাদি অবগত হয়ে দুঃখজনক অতীতের পুনরাবৃত্তি প্রতিরোধ এবং ইতিবাচক অর্জনের ধারা অব্যাহত রাখার চেষ্টা জোরদার করে তুলতে পারি। তা করতে গেলে আমরা দেখতে পাব, ভাষা আন্দোলন আমাদের প্রিয় স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এক অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করেছে।
তবে ইতিহাসেরও যেমন ইতিহাস থাকে, তেমনি ভাষা আন্দোলনেরও একটি ঐতিহাসিক পটভূমি ছিল। সেই পটভূমি ছাড়া ভাষা আন্দোলন সৃষ্টি করা সম্ভব হতো না। তাই ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া আমাদের জাতির সঠিক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস জানার স্বার্থেই অপরিহার্য। এ কথা ইতিহাসবিদ মাত্রই জানেন যে, ১৭৫৭ সালে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজুদ্দৌল্লার দরবারের কতিপয় বিশ্বাসঘাতক সদস্যের সাথে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গোপন যোগাযোগের মাধ্যমে পলাশীতে সিরাজুদ্দৌলার পরাজয়বরণ ও নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে এদেশে ইংরেজদের রাজত্ব শুরু হয়। বিদেশি নব্য শাসক ইংরেজরা গোড়া থেকেই সুপরিকল্পিতভাবে একটি নীতি অনুসরণ করে চলে। তারা প্রশাসন, প্রতিরক্ষা, জমিদারি, ভূমি ব্যবস্থা, শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভৃতি সকল গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র থেকে বেছে বেছে মুসলমানদের উৎখাত করে সেখানে ইংরেজ অনুগত হিন্দুদের বসানোর নীতি অনুসরণ করে চলে। পলাশী বিপর্যয়ের অল্প কয়েক বছর পর ১৭৯৩ সালে নব্য শাসকরা পুরাতন ভূমি ব্যবস্থা পরিবর্তন করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে যে নতুন ভূমি ব্যবস্থা প্রবর্তন করে তার বদৌলতে ইংরেজ ভক্ত এমন এক নব্য জমিদার গোষ্ঠী গড়ে ওঠে, যার সিংহভাগই ছিল হিন্দু।
মুসলমানরাও বিদেশি শাসকদের কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। তারা ১০০ বছর ধরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যান মীর কাশেম, টিপু সুলতান, মজনু শাহ, শরীয়তুল্লাহ, সৈয়দ আহমেদ ব্রেলভী, তিতুমীর, দুদু মিয়া প্রমুখের নেতৃত্বে। এই সংগ্রামের সর্বশেষ পর্ব ছিল ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ। কিন্তু বৃহত্তর প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের অসহযোগিতা ও ইংরেজ তোষণ নীতির কারণে এর সকল সংগ্রামই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সর্বশেষ পর্যায়ে সিপাহি বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার পর মুসলমানদের ওপর নির্যাতনে খড়গ নতুনভাবে নেমে আসে।
এ পরিস্থিতিতে মুসলমানদের সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে উত্তর ভারতের স্যার সৈয়দ আহমদ খান, বাংলার নবাব আবদুল লতিফ প্রমুখ তদানীন্তন মুসলিম নেতৃবৃন্দ সাময়িকভাবে ইংরেজদের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে হিন্দু নেতৃবৃন্দের মতো আধুনিক শিক্ষায় মুসলমানদের শিক্ষিত ও উন্নত করে তোলার নীতি গ্রহণ করেন। এই সহযোগিতা যুগের শেষ দিকের অন্যতম নেতা ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহর আমলে ১৯০৫ সালে প্রধানত প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে বাংলা বিহার উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত বিশাল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিকে বিভক্ত করে ঢাকা রাজধানীসহ ‘পূর্ববঙ্গ ও আসাম’ নামে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করা হয়। এতে দীর্ঘ অবহেলিত পূর্ববঙ্গের উন্নতির কিঞ্চিত সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় বলে নবাব সলিমুল্লাহ এর প্রতি সমর্থন দান করেন।
কিন্তু এই বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ববঙ্গে অবস্থিত জমিদারিতে কলকাতার প্রবাসী জমিদারদের প্রভাব হ্রাসের আশঙ্কায় কলকাতা প্রবাসী হিন্দু জামিদাররা এর বিরুদ্ধে বিরাট আন্দোলন গড়ে তোলেন। পলাশী হতে এ পর্যন্ত যে হিন্দু নেতৃবৃন্দ সব সময় ইংরেজদের পক্ষাবলম্বন করে এসেছে, তাদের আকস্মিক এ রুদ্রমূর্তি ইংরেজদের ভাবিয়ে তোলে। ফলে মাত্র ছয় বছরের মাথায় এ ব্যবস্থা বাতিল ঘোষণা করে ইংরেজরা তাদের পুরাতন মিত্রদের মনস্তুষ্টির প্রয়াস পায়।
সহযোগিতা যুগের অন্যতম নেতা নবাব সুলিমুল্লাহ বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। তাঁর এ ক্ষোভ প্রশমনার্থে ইংরেজ সরকার তাঁর অন্যতম দাবি ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করে। এতেও কলকাতা প্রবাসী বুদ্ধিজীবীদের ঘোরতর আপত্তি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গড়ের মাঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তাদের বক্তব্য ছিল, তার দ্বারা নাকি বঙ্গমাতাকে দিখ-িত করার মতো পাপ হবে। এবার তাদের যুক্তি হলো, এর দ্বারা বঙ্গ সংস্কৃতি দ্বিখ-িত করা হবে। তবে তারা আরেকটা যে যুক্তি (কুযুক্তি!) দিল তার মাধ্যমে তাদের আসল মনোভাব বড় নোংরাভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ল। তাদের এ যুক্তি হলো : পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ মানুষ অশিক্ষিত মুসলমান চাষাভূষা, তাদের উচ্চশিক্ষার জন্য ঢাকায় কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের মুসলমান চাষাভূষারা অশিক্ষিত আছে তাই থাকুক, তাদের শিক্ষিত বা উচ্চশিক্ষিত করে তোলার কোনো প্রয়োজন নেই।
এসব বিরোধিতার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ১০ বছর পিছিয়ে যায়। ১৯২১ সালে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতাকারীদের কারণে এ বিশ্ববিদ্যালয় হয় আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর কর্তৃত্ব থাকে ঢাকা নগরীর স্কুল কলেজের মধ্যে সীমাবদ্ধ। পূর্ববঙ্গের অন্য সমস্ত স্কুল-কলেজ আগের মতো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্বাধীন থাকে। পূর্ববঙ্গের অন্যান্য স্কুল-কলেজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব থেকে মুক্তি পায় ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর।
এবার ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গে ফিরে আসছি। ভাষা আন্দোলন যে পটভূমিতে শুরু হয়, তার জন্য সাতচল্লিশের পার্টিশন ছিল অপরিহার্য। ১৯৪৭ সালে যদি ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষ অখ- ভারত হিসেবে স্বাধীন হতো, তা হলে অবিভক্ত ভারতে হিন্দি ভাষাভাষীদের বিপুল সংখ্যাধিক্যের কারণে এবং ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের হিন্দি ভাষার প্রতি প্রবল সমর্থনের কারণে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবির কথা কল্পনা করাও সম্ভবপর হতো না। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষ ভারত ও পাকিস্তান নামের দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে স্বাধীন হওয়ার ফলে সমগ্র পাকিস্তানের ৫৬% অধিবাসী বাংলাভাষী হওয়াতেই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তোলা সম্ভব হয়।
এখানে আরেকটি প্রসঙ্গও স্বাভাবিক কারণে আলোচিত হতে পারে। উপমহাদেশের সকল বাংলাভাষী অঞ্চল নিয়ে স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কি সম্ভব ছিল না? এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, সম্ভব ছিল এবং বাস্তবেও ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তানের বাইরে একটি সার্বভৌম বৃহত্তর বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি জানানো হয়েছিল মুসলিম লীগের হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম এবং কংগ্রেসের শরৎচন্দ্র বসুর মাধ্যমে। আমরা দৈনিক ইত্তেফাক-এর বিশেষ সোহরাওয়ার্দী সংখ্যার কল্যাণে জানতে পারি এ প্রচেষ্টার প্রতি মুসলিম লীগ নেতা কায়েদে আজম জিন্নাহর সমর্থনও ছিল। কিন্তু গান্ধী, নেহরু, প্যাটেল প্রমুখ অবাঙালি হিন্দু নেতা এবং শ্যামা প্রসাদ প্রমুখ বাঙালি হিন্দু নেতার প্রবল বিরোধিতার কারণে সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। সে সময় শেষোক্ত বাঙালি নেতা শ্যামা প্রসাদ এমনও বলেছিলেন, ভারত ভাগ না হলেও বাংলা ভাগ হতেই হবে। নইলে বাঙালি হিন্দুরা চিরতরে বাঙালি মুসলমানদের গোলাম হয়ে যাবে। অর্থাৎ তাঁর কাছে বাঙালি মুসলমানদের তুলনায় অবাঙালি হিন্দুদের অধীনতা অনেক পছন্দনীয় ছিল। এতে আরও বোঝা যায়, ১৯০৫ সালে বঙ্গবঙ্গের বিরুদ্ধে তারা একে বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ করার মতো পাপ বলেছিলেন, তা ছিল নেহায়েত রাজনৈতিক চাতুর্যের বহিঃপ্রকাশ।
উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, সাতচল্লিশের পার্টিশনের কাছে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের অশেষ ঋণ রয়েছে এবং সাতচল্লিশের পার্টিশন না হলে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তোলা সম্ভবপরই হতো না। আর বাস্তবেও দেখা যায়, যারা সাতচল্লিশের পার্টিশনের জন্য আন্দোলন করেছিলেন, তারাই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। তবে পাকিস্তানের উচ্চপদস্থ আমলাদের মধ্যে উর্দুভাষীদের প্রবল সংখ্যাধিক্যের সুযোগে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার গোপন একটা প্রচেষ্টা শুরু হয়ে যায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার গোড়ার দিক থেকেই। তার প্রমাণ পাওয়া যায় নতুন রাষ্ট্রের পোস্টকার্ড, এনভেলপ, মানি অর্ডার ফরম প্রভৃতিতে ইংরেজির পাশাপাশি শুধু উর্দুর ব্যবহারের মাধ্যমে। এই পটভূমিতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক আবুল কাসেমের উদ্যোগে ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠিত তমদ্দুন মজলিস নামের সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে ১৫ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত ‘পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু’ শীর্ষক পুস্তিকার মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসেই তমদ্দুন মজলিসের অন্যতম সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিজ্ঞানের অধ্যাপক নুরুল হক ভুইয়াকে কনভেনর করে প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। তমদ্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম (পরবর্তীকালে মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান), সাংস্কৃতিক সংগঠক শামসুল আলম, ফজলুর রহমান ভুঁইয়া (আওয়ামী লীগ প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত ১৯৭০ সালের এমপি) প্রমুখ।
১৯৪৭ সালে ভাষা আন্দোলন পরিচালিত হয় এককভাবে তমদ্দুন মজলিসের নেতৃত্বে। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থক ছাত্র প্রতিষ্ঠান মুসলিম ছাত্রলীগের একটি অংশ পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ নামে আত্মপ্রকাশ করে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ওই ছাত্র সংস্থা তমদ্দুন মজলিস-সূচিত ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। এই সংস্থা ভাষা আন্দোলনের প্রতি সমর্থন প্রকাশের পর তমদ্দুন মজলিস ও এই ছাত্রলীগের যুগপৎ সদস্য শামসুল আলমকে কনভেনর করে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এ সময় করাচিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান গণপরিষদে কংগ্রেস দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলাতে বক্তৃতাদানের অধিকার দাবি করলে সে দাবি প্রত্যাখ্যাত হয়। তার রিুদ্ধে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিবাদ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয়।
১১ মার্চের সে প্রতিবাদ দিবস বিপুল সাফল্যম-িত হয়। সেক্রেটারিয়েটের বিভিন্ন গেটে পিকেটিং করা হয়। পুলিশ অনেক পিকেটারকে গ্রেফতার করে। পিকেটারদের অনেকে পুলিশের লাঠিচার্জে আহত হন। এসব খবর ঢাকা শহরের বিভিন্নœ এলাকায় পৌঁছে গেলে সেসব এলাকা থেকে আসা লোকদের মাধ্যমে সেক্রেটারিয়েট এলাকা অচিরেই বিক্ষুব্ধ জনসমুদ্রে পরিণত হয়। সমগ্র এলাকায় এভাবে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। ১১ থেকে ১৫ মার্চ পর্যন্ত এ অচলাবস্থা চলতে থাকায় প্রাদেশিক চিফ মিনিস্টার খাজা নাজিমুদ্দিন ১৫ মার্চ ভাষা সংগ্রাম পরিষদের সকল দাবি-দাওয়া মেনে চুক্তিস্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। এতে অবস্থা সাময়িকভাবে শান্ত হয়ে আসে। যে নাজিমুদ্দিন ১৯৪৮ সালের ১৫ মার্চ ভাষা আন্দোলনের সকল দাবি-দাওয়া মেনে নিয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করেন, তিনি ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঢাকায় এসে এক জনসভায় উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করায় জনগণ একে তার চরম বিশ্বাসঘাতকতা বলে বিবেচনা করে তার প্রতিবাদে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিবাদ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই প্রতিবাদ দিবস ব্যর্থ করে দিতে সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি হঠাৎ ১৪৪ ধারা জারি করে বসে। ২১ ফেব্রুয়ারি সরকারের এ অপচেষ্টার বিরুদ্ধে বাংলার মাতৃভাষাপ্রমী তরুনরা বুকের রক্ত দিয়ে সরকারের বাংলাভাষা বিরোধী চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়ে বাংলার দাবিকে প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে ভাষা আন্দোলনের পথ বেয়েই মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। ভাষা আন্দোলনের স্মারক মাসে আজ প্রশ্ন জাগে, রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার যে লক্ষ্যে ভাষা আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল তার প্রতি আমরা কতটা আমাদের দায়িত্ব পালন করছি।
![]() দৈনিক ইনকিলাব সংবিধান ও জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাই ধর্ম ও রাষ্ট্রবিরোধী এবং উষ্কানীমূলক কোনো বক্তব্য না করার জন্য পাঠকদের অনুরোধ করা হলো। কর্তৃপক্ষ যেকোনো ধরণের আপত্তিকর মন্তব্য মডারেশনের ক্ষমতা রাখেন।
দৈনিক ইনকিলাব সংবিধান ও জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাই ধর্ম ও রাষ্ট্রবিরোধী এবং উষ্কানীমূলক কোনো বক্তব্য না করার জন্য পাঠকদের অনুরোধ করা হলো। কর্তৃপক্ষ যেকোনো ধরণের আপত্তিকর মন্তব্য মডারেশনের ক্ষমতা রাখেন।